বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর নাম,
বাংলাদেশের ছেলে তুমি হুগলী জেলায় ধাম। (অধুনা মেদিনীপুর )
মাতা তোমার ভগবতী ,পিতা ঠাকুরদাস ,
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার। তাঁর প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই লাভ করেন বিদ্যাসাগর উপাধি। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি ছিল তাঁর। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ করে তোলেন ও অপরবোধ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। রচনা করেছেন জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় সহ, একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা।
অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম আজও স্মরিত হয় যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বাংলার নবজাগরণের এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন ‘দয়ার সাগর’ নামে। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত কখনই তাঁর দ্বার থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। এমনকি নিজের চরম অর্থসংকটের সময়ও তিনি ঋণ নিয়ে পরোপকার করেছেন। তাঁর পিতামাতার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মশক্তি ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।
বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় স্থাপিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানী কলকাতার আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিদ্যাসাগর সেতু তাঁরই নামে উৎসর্গিত।
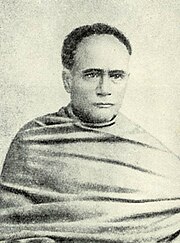
বাংলাদেশের ছেলে তুমি হুগলী জেলায় ধাম। (অধুনা মেদিনীপুর )
মাতা তোমার ভগবতী ,পিতা ঠাকুরদাস ,
তুমিই মোদের গুরুর গুরু ,পুরাও মোদের আশ।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২২৭
বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন) বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে
জন্মগ্রহণ করেন। বীরসিংহ সেই সময় হুগলি জেলার
অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন সুপণ্ডিত ও
বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা পুরুষ। ইনিই ঈশ্বরচন্দ্রের নামকরণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের
পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় সামান্য চাকুরি করতেন। পরিবার
নিয়ে শহরে বাস করা তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। সেই কারণে বালক ঈশ্বরচন্দ্র
গ্রামেই মা ভগবতী দেবী ও ঠাকুরমার সঙ্গে বাস করতেন।
অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম আজও স্মরিত হয় যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বাংলার নবজাগরণের এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন ‘দয়ার সাগর’ নামে। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত কখনই তাঁর দ্বার থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। এমনকি নিজের চরম অর্থসংকটের সময়ও তিনি ঋণ নিয়ে পরোপকার করেছেন। তাঁর পিতামাতার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মশক্তি ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।
বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় স্থাপিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানী কলকাতার আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিদ্যাসাগর সেতু তাঁরই নামে উৎসর্গিত।
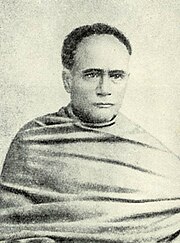
| জন্ম তারিখ: | সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০ | ||
|---|---|---|---|
| জন্মস্থান: | বীরসিংহ, তদনীন্তন হুগলি জেলা (অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা), বাংলা প্রেসিডেন্সি (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ), ব্রিটিশ ভারত (অধুনা |
||
| মৃত্যু তারিখ: | জুলাই ২৯, ১৮৯১ (৭০ বছর) | ||
| মৃত্যুস্থান: | কলকাতা, বাংলা প্রেসিডেন্সি (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ), ব্রিটিশ ভারত (অধুনা |
||
| জীবনকাল: | সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০ – জুলাই ২৯, ১৮৯১ | ||
| আন্দোলন: | বাংলার নবজাগরণ | ||
| প্রধান স্মৃতিস্তম্ভ: | বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর সেতু | ||
| ধর্ম: | হিন্দু | ||
| দাম্পত্য সঙ্গী: | দীনময়ী দেবী | ||
পিতামাতা:
|
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবী নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন |
||
শিক্ষাজীবনচার বছর নয় মাস বয়সে ঠাকুরদাস বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু সনাতন বিশ্বাস বিদ্যাদানের চেয়ে শাস্তিদানেই অধিক আনন্দ পেতেন। সেই কারণে রামজয় তর্কভূষণের উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক উৎসাহী যুবক বীরসিংহে একটি নতুন পাঠশালা স্থাপন করেন। আট বছর বয়সে এই পাঠশালায় ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর চোখে কালীকান্ত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। কালীকান্তের পাঠশালায় তিনি সেকালের প্রচলিত বাংলা শিক্ষা লাভ করেছিলেন।১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তাঁদের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন কালীকান্ত ও চাকর আনন্দরাম গুটিও। কথিত আছে, পদব্রজে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় পথের ধারে মাইলফলকে ইংরেজি সংখ্যাগুলি দেখে তিনি সেগুলি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত করেছিলেন। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের বিখ্যাত সিংহ পরিবারে তাঁরা আশ্রয় নেন। এই পরিবারের কর্তা তখন জগদ্দুর্লভ সিংহ। ১৮২৯ সালের ১ জুন সোমবার কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮২৪ সালে; অর্থাৎ, ঈশ্বরচন্দ্রের এই কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর আগে। তাঁর বয়স তখন নয় বছর। এই কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও নদিয়া-নিবাসী মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগরের আত্মকথা থেকে জানা যায় মোট সাড়ে তিন বছর তিনি ওই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ পড়ার সময় ১৮৩০ সালে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণীতেও ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৩১ সালের মার্চ মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি এবং ‘আউট স্টুডেন্ট’ হিসেবে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ ও আট টাকা পারিতোষিক পান। সংস্কৃত কলেজে মাসিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের ‘পে স্টুডেন্ট’ ও অন্য ছাত্রদের ‘আউট স্টুডেন্ট’ বলা হত। অন্যদিকে তিন বছর ব্যাকরণ শ্রেণীতে পঠনপাঠনের পর বারো বছর বয়সে প্রবেশ করেন কাব্য শ্রেণীতে। সে যুগে এই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ১৮৩৩ সালে ‘পে স্টুডেন্ট’ হিসেবেও ঈশ্বরচন্দ্র ২ টাকা পেয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে ইংরেজি ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ৫ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক হিসেবে পান। এই বছরই ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রূপে পলিটিক্যাল রিডার নং ৩ ও ইংলিশ রিডার নং ২ পারিতোষিক পান। এই বছরই নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি শ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বর্ষে সাহিত্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পনেরো বছর বয়সে প্রবেশ করেন অলংকার শ্রেণীতে। অলংকার শাস্ত্র একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তিনি সাহিত্য দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলংকার গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৩৬ সালে অলংকার পাঠ শেষ করেন। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রঘুবংশম্, সাহিত্য দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, মালতী মাধব, উত্তর রামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী ও মৃচ্ছকটিক গ্রন্থ পারিতোষিক পান। ১৮৩৭ সালের মে মাসে তাঁর ও মদনমোহনের মাসিক বৃত্তি বেড়ে হয় আট টাকা। এই বছরই ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই যুগে স্মৃতি পড়তে হলে আগে বেদান্ত ও ন্যায়দর্শন পড়তে হত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মেধায় সন্তুষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরাসরি স্মৃতি শ্রেণীতে ভর্তি নেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন এবং হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ত্রিপুরায় জেলা জজ পণ্ডিতের পদ পেয়েও পিতার অনুরোধে তা প্রত্যাখ্যান করে ভর্তি হন বেদান্ত শ্রেণীতে। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি সেই সময় বেদান্তের অধ্যাপক। ১৮৩৮ সালে সমাপ্ত করেন বেদান্ত পাঠ। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মনুসংহিতা, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, অষ্টবিংশতত্ত্ব, দত্তক চন্দ্রিকা ও দত্তক মীমাংসা গ্রন্থ পারিতোষিক পান। সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৪০-৪১ সালে ন্যায় শ্রেণীতে পঠনপাঠন করেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই শ্রেণীতে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে তিনি পারিতোষিক পান। ন্যায় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে ১০০ টাকা, পদ্য রচনার জন্য ১০০ টাকা, দেবনাগরী হস্তাক্ষরের জন্য ৮ টাকা ও বাংলায় কোম্পানির রেগুলেশন বিষয়ক পরীক্ষায় ২৫ টাকা – সর্বসাকুল্যে ২৩৩ টাকা পারিতোষিক পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর উপাধি লাভজন্ম গ্রহন কালে তার পিতামহ তার বংশানু্যায়ী নাম রেখেছিলেন "ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"। ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই পরীক্ষাতেও যথারীতি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৬ মে ল কমিটির কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান, তাতেই প্রথম তাঁর নামের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহৃত হয়। এই প্রশংসাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :
HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION
We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of
Fort William on the 22nd Twenty-second April 1839 by the Committee
appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chandra
Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent
knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law officer in
any of the Established Courts of Judicature.
H.T. Prinsep President J.W.J. Ousely Member of the Committee of Examination This Certificate has been granted to the said Issur Chandra Vidyasagar under the seal of the committee. This 16th Sixteenth day of May in the year 1839 Corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda. J.C.C. Sutherland Secy To the Committee সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর তিনি এই কলেজ থেকে অপর একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত দেবনাগরী হরফে লিখিত এই সংস্কৃত প্রশংসাপত্রে কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত করেন। প্রশংসাপত্রটি নিম্নরূপ:
অস্মাভিঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলকাতায়াং
শ্রীযুত কোম্পানী সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫
পঞ্চমাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রান্য ধীতবান্
কাম্যশাস্ত্রম্... শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ অলঙ্কারশাস্ত্রম্... শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ বেদান্তশাস্ত্রম্... শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ ন্যায়শাস্ত্রম্... শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রম্... শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ ধর্মশাস্ত্রম্... শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ সুশীলতয়োপস্থিতস্বৈত স্বৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতি দিবসীয়ম্। Rasamoy Dutt. Secretary. 10 Decr 1841. | |||








































